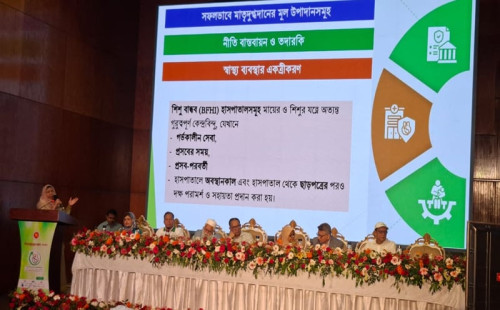তিন মাসে তারল্য কমেছে ২৭,১৫১ কোটি টাকা

অস্বাভাবিকভাবে
কমেছে ব্যাংক খাতের তারল্য। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই তিন
মাসে তারল্য কমেছে ২৭ হাজার ১৫১ কোটি টাকা।
গত বছরের জুন শেষে ব্যাংকে মোট তারল্য ছিল ৪ লাখ ৩১ হাজার ৯২৯ কোটি টাকা। গত ৩০
সেপ্টেম্বর তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৪ হাজার ৭৭৮ কোটি টাকায়। তবে গত অক্টোবরে এসে
তারল্য কিছুটা বেড়েছে।ওই সময়ে মোট
তারল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ১৫ হাজার ৫৩৫ কোটি টাকায়। এ হিসাবে গত জুলাই থেকে
অক্টোবর পর্যন্ত এই চার মাসে তারল্য কমেছে ২৬ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। বাংলাদেশ
ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।
প্রতিবেদনে
ব্যাংকিং খাতে তারল্য কমার জন্য চারটি কারণকে শনাক্ত করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
এগুলো হচ্ছে-করোনার পর হঠাৎ করে চাহিদা বৃদ্ধি, বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহে বাড়তি
প্রবৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বাড়ার কারণে আমদানি ব্যয়ের
মাত্রাতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি ও ব্যাংক থেকে নগদ টাকা তুলে গ্রাহকরা নিজেদের হাতে রাখার
প্রবণতা বেড়ে যাওয়া।
সূত্র
জানায়, এসব কারণের বাইরেও ব্যাংকিং খাতে তারল্য কমার আরও কিছু কারণ রয়েছে।
সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ‘ব্যাংকিং
খাতে টাকা নেই’। এ ধরনের গুজবের শিকার হয়ে ব্যাংক থেকে অনেকে টাকা তুলে নিয়েছেন। এ
পরিস্থিতিতে ব্যাংকিং খাতে তারল্যের জোগান স্বাভাবিক রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে
নগদ টাকার জোগান বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে মুদ্রানীতির বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে
ব্যাংকগুলোর চাহিদা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে প্রায়
প্রতিদিনই। কোনো কোনোদিন ১৩ হাজার কোটি টাকারও জোগান দেওয়া হয়েছে। এর বিপরীতে অনেক
উপকরণের মেয়াদ শেষ হওয়ায় ওইসব অর্থ ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ফেরত দিয়ে নতুন
করে টাকা নিয়েছেন। এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।
সূত্র
জানায়, ডলারের দাম ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বাড়ায় আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির
কারণে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের জোগান বেড়েছে। আমদানি ব্যয় মেটাতে ব্যাংকগুলোকে
ডলার দিতে হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি খাতে ঋণ বাড়ায় ও গ্রাহকরা নগদ টাকা তুলে নেওয়ায়
সার্বিকভাবে ব্যাংকে তারল্য কমেছে। এদিকে ব্যাংকের আমানত, রপ্তানি আয় ও
রেমিট্যান্স কমায় নতুনভাবে তারল্যের জোগান কমেছে। এসব মিলে ব্যাংকিং খাতে তারল্য
কমেছে।
কেন্দ্রীয়
ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২০ সালের জুন থেকে ব্যাংকিং খাতে তারল্য
পরিস্থিতি বাড়তে থাকে। ওই বছরের জুনে তারল্য ছিল ৩ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা। একই
বছরের সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে ৩ লাখ ৫২ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ওই বছরের ডিসেম্বরে
তা আরও বেড়ে ৪ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। করোনার কারণে ওই সময়ে ঋণপ্রবাহ কমে যাওয়া
ও আমানত বাড়ার কারণে তারল্য বেড়েছিল। ২০২১ সালের মার্চে তারল্য ২০২০ সালের
ডিসেম্বরের তুলনায় কিছুটা বেড়েছিল। ২০২১ সালের জুনে এসে তারল্য আরও বেড়ে ৪ লাখ ৩৮
হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে তারল্য ছিল ৪ লাখ ৩৪ হাজার কোটি
টাকা। ওই বছরের ডিসেম্বরে সামান্য বেড়ে ৪ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চলতি
বছরের জানুয়ারি থেকে তারল্য কমতে থাকে। মার্চে কমে ৪ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকায় নামে।
জুনে সামান্য বেড়ে ৪ লাখ ৩২ হাজার কোটি টাকা হয়। সেপ্টেম্বরে তা আরও কমে ৪ লাখ ৫
হাজার কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তবে অক্টোবরে কিছুটা বেড়ে ৪ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা
হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং খাতে তারল্য
পরিস্থিতি এভাবে কখনো কমেনি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অপর একটি প্রতিবেদন থেকে পাওয়া
তথ্যে দেখা যায়, গত জুনে ব্যাংকিং খাতে মোট তারল্য ছিল ৪ লাখ ৪১ হাজার ৬৮২ কোটি
টাকা। এ হিসাবে গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে তারল্য কমেছে ৩৬ হাজার ৯০৪ কোটি
টাকা। গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের হিসাবে এক বছরে
তারল্য কমেছে ২৮ হাজার ৮১৬ কোটি টাকা। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন
কর্মকর্তা জানান, ব্যাংকিং খাতে তারল্য পরিস্থিতি সব সময়ই ওঠানামা করে। এটি বিশেষ
করে ব্যাংকগুলোর আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা জুন ও ডিসেম্বরভিত্তিক সময়ের সঙ্গে
তুলনা করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এ কারণে জুন ও ডিসেম্বরে আমানত বেড়ে যায়।
মার্চ ও সেপ্টেম্বরে তা কিছুটা কমে যায়।
তিনি আশা
প্রকাশ করে বলেন, তারল্য পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে। সেপ্টেম্বরের তুলনায়
অক্টোবরে তারল্য বেড়েছে। ডিসেম্বরে গিয়ে তা আরও বাড়বে। কারণ ওই সময়ে আমানত বাড়াতে
ব্যাংকগুলো নানা পদক্ষেপ নেয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেও বাণিজ্যিক
ব্যাংকগুলোকে চাহিদা অনুযায়ী তারল্যের জোগান দেওয়া হচ্ছে।
ডিসেম্বরের
শুরুর দিকে প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস বাংলাদেশ উন্নয়ন
গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক সেমিনারে বলেছিলেন, ‘গুজব
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রাহকরা ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছিলেন। সেই
টাকা ফেরত আসতে শুরু করেছে।’
কেন্দ্রীয়
ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর
অতিরিক্ত তারল্য কমেছে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা।
সূত্র
জানায়, ব্যাংকিং খাতে ডলার সংকটের কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমদানি ব্যয় ও
বৈদেশিক ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছিল না। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ডলারের
জোগান দেওয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ৭৬২ কোটি ডলার বিক্রি করেছে। এর
বিপরীতে ক্রয় করেছে মাত্র ২১ কোটি ডলার। চলতি অর্থবছরের জুলাই সেপ্টেম্বরে
কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজার থেকে কোন ডলার ক্রয় করেনি। উলটো ৩৫৬ কোটি ২৩ লাখ ডলার
বিক্রি করেছে। এর আগে গত এপ্রিল থেকে জুন সময়ে বিক্রি করেছিল ৩৫৮ কোটি ডলার। এ
হিসাবে গত এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে বিক্রি করেছে ৭১৪ কোটি ডলার। এ
খাতে প্রায় ৭১ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চলে গেছে। তারল্য
সংকটের এটিও একটি কারন। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় কমেছে।
বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ কমার কারণেও টাকার প্রবাহ কমেছে।
গত
অর্থবছরের প্রথম দিকে ডলারের সংকট তেমন একটা ছিল না। গত এপ্রিল থেকে সংকট প্রকট
হতে শুরু করে। এ কারণে গত পুরো অর্থবছরের তুলনায় গত ছয় মাসে প্রায় সমান ডলার
বিক্রি করা হয়েছে। এদিকে গত ১ জুলাই থেকে গত ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংক
রিজার্ভ থেকে ৬১০ কোটি ডলার বিক্রি করেছে। এ হিসাবে গত অর্থবছর থেকে চলতি
অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ১ হাজার ৩৭২ কোটি
ডলার বিক্রি করেছে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে।
একই সময়ে
ডলারের বিপরীতে টাকার বড় ধরনের অবমূল্যায়ন হয়েছে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতি
ডলার ছিল ৮৪ টাকা ৮৪ পয়সা। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৫ টাকা ৫০
পয়সা। ওই এক বছরে ডলারের দাম বেড়েছে ৬৬ পয়সা। গত সেপ্টেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬
টাকা। ওই দুই বছরে ডলারের দাম বেড়েছে ১১ টাকা ১৬ পয়সা। বর্তমানে ডলার সর্বোচ্চ
বিক্রি হচ্ছে ১০৭ টাকা করে। এ হিসাবে দাম বেড়েছে ২২ টাকা ১৬ পয়সা।
চলতি বছরের
এপ্রিল থেকেই ডলারের দাম বেশি বেড়েছে। গত এপ্রিলের শুরুতে প্রতি ডলারের দাম ছিল ৮৬
টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১০৭ টাকা। গত আট মাসে ডলারের দাম বেড়েছে ২১ টাকা।
ডলারের দাম
ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম বাড়ায় আমদানি ব্যয় বেড়েছে লাগামহীনভাবে। গত
অর্থবছরে আমদানি ব্যয় বেড়েছিল প্রায় ৪৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
বেড়েছে ৮ শতাংশ। গত অর্থবছরে বেসরকারি খাতে ঋণ বেড়েছিল ৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেড়েছে ১৪ শতাংশ।